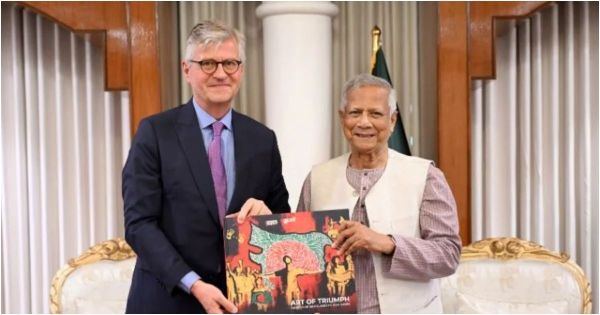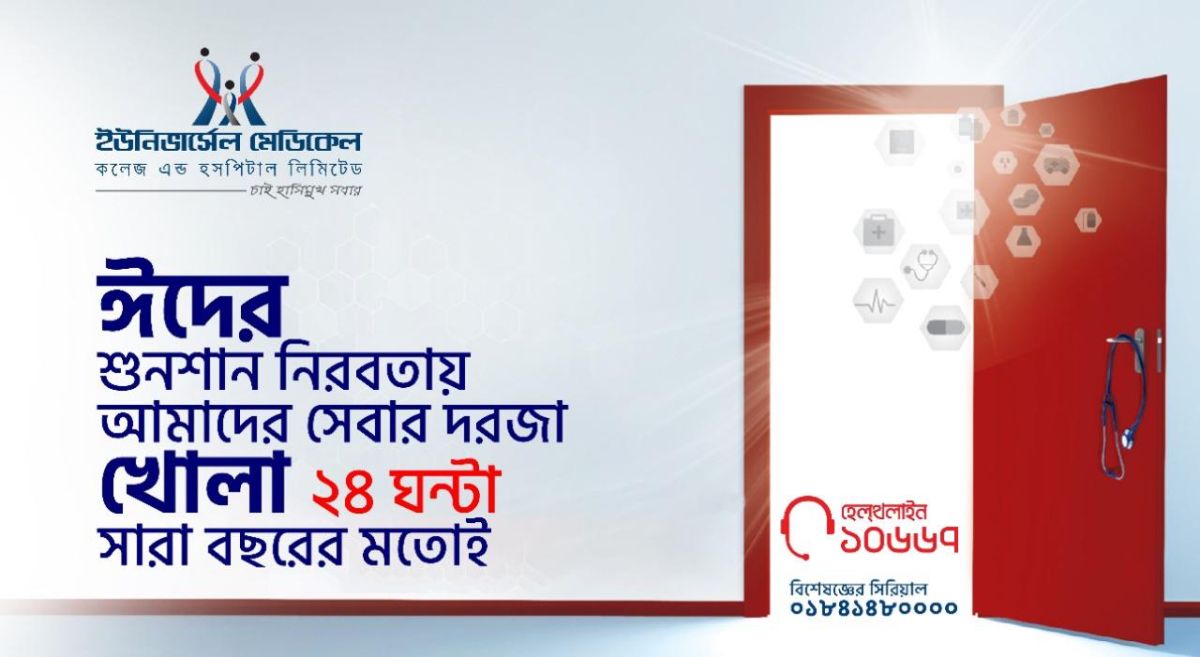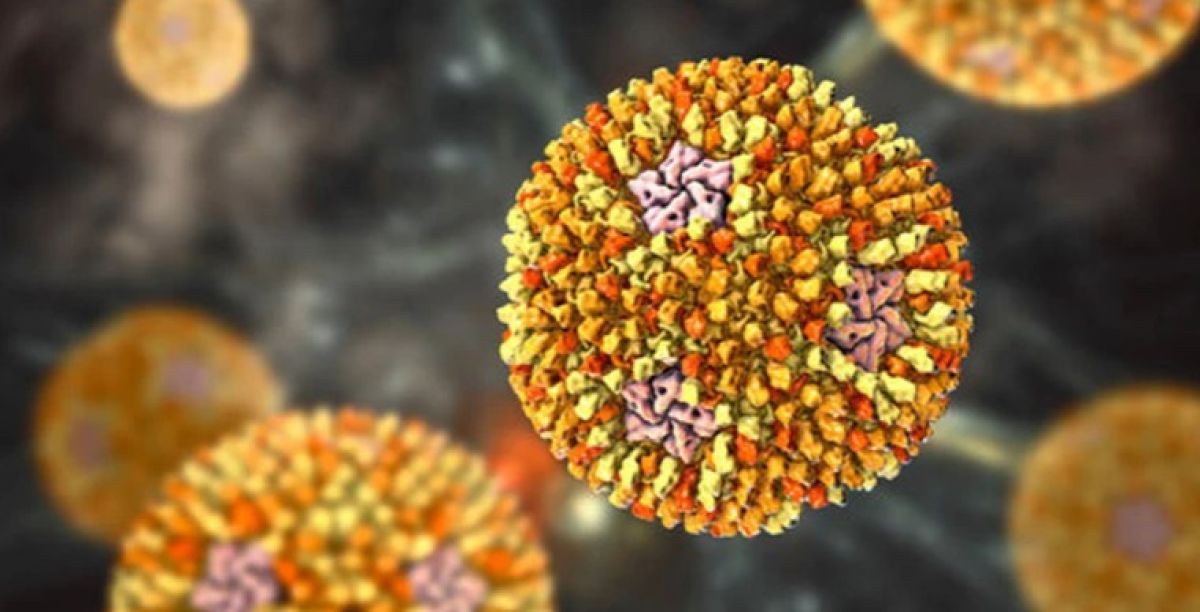ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা ৯ দিন ছুটিতে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও ব্যাংক বন্ধ থাকলেও হাসপাতাল বন্ধ রাখার সুযোগ নেই। ঈদের সময় হাসপাতালগুলোতে রোগীরা আদৌ কাঙ্ক্ষিত সেবা পান কিনা এবং কোন প্রক্রিয়ায় এ সেবা দেওয়া হয়—সেসব নিয়ে অনেকের মধ্যে কৌতূহল জাগে।
ঈদের ছুটিতে সরেজমিনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি হাসপাতালেই পর্যাপ্ত রোগী আছে। যদিও ছুটির এ সময়ে অধ্যাপক পর্যায়ের চিকিৎসকদের পদচারণা কম; তবে রোগীদের ভাষ্যমতে, মেডিকেল অফিসার ও জুনিয়র ডাক্তাররা তাদের খোঁজ খবর রাখছেন; আছেন নার্সরাও।
রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, ঈদের দিন প্রায় ৫০০’র মতো রোগী আছে হাসপাতালটিতে। এদের মধ্যে অনেকের শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় দেওয়া হয়নি ছাড়পত্র। ঈদের সময় জ্যেষ্ঠ ডাক্তাররা আসবেন কিনা বা এই সময়ে কতটুকু চিকিৎসাবা পাবেন—এ নিয়ে চিন্তার ভাঁজ রোগীদের কপালে।
কিডনিতে পাথর নিয়ে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সোহরাওয়ার্দীতে ভর্তি আছেন হবিগঞ্জ জেলার আহাদ মিয়া (৬০)।
পেশায় দিনমজুর আহাদ বলেন, ‘ডাক্তার কিডনি ওয়াশ করছে। তবে এখনও কিছু পাথর আছে। ডাক্তারই বলছে ঈদ এখানে করতে। এখন পর্যন্ত চিকিৎসায় কোনো ঘাটতি হয় নাই। ঈদের এ কয়দিনের ছুটিতে ডাক্তার রেগুলার আসছে। দেখি সামনের দিনগুলাতে কী হয়!’
বরগুনা থেকে মূত্রথলিতে টিউমার নিয়ে ২০ দিন ধরে হাসপাতালে আছেন সফেদ হাওলাদার (৭২)। এবারের ঈদ তাকে হাসপাতালেই কাটাতে হয়েছে। চিকিৎসকরা আগামী ৫ এপ্রিল ঈদের ছুটির মধ্যেই তার অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান সফেদের মেয়ে পারভীন আক্তার (৪০)।
তিনি বলেন, ‘ঈদের এ কয়দিনের ছুটিতেও ভালো সেবা পাচ্ছি। তবে বড় ডাক্তার না থাকায় ঈদের পর অপারেশন হবে। আগের থেকে আব্বার অবস্থা এখন অনেকটাই ভালো।’
ঈদের সময় ডাক্তার-নার্স কম থাকা নিয়ে হাসপাতালটির সিনিয়র স্টাফ নার্স সাধনা হালদার বলেন, ‘অন্যান্য সময়ের থেকে ঈদের ছুটির এ সময়ে হাসপাতালে ডাক্তার-নার্স স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কম থাকে। তবে এটা ভাবার কারণ নেই যে, হাসপাতাল নার্স-ডাক্তারশূন্য থাকবে। যেকোনো রোগীর জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সার্বক্ষণিক একজন ডাক্তার মজুত থাকেন। ঈদের নামাজের সময় বা দুপুরের দিকে অন্য ধর্মাবলম্বী ডাক্তার-নার্সরা ডিউটি করেন। এতে করে সংকটময় কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না।’
হাসপাতালটির আরেক সিনিয়র স্টাফ নার্স বিউটি গোমেজ বলেন, ‘ঈদের আগে অনেকেই নিজ থেকে রিলিজ চায়। তবে সিরিয়াস রোগীদের রিলিজ দেওয়ার সুযোগ নেই। ওষুধ দেওয়া, ড্রেসিং করানো, ইনজেকশন পুশের মতো কাজ রোগী বাসায় নিজে করতে পারবে না, আবার এর জন্য তার সিনিয়র ডাক্তারদেরও প্রয়োজন নেই। হাসপাতালে থাকলে প্রাথমিক সেবাগুলো নার্স ও মেডিকেল অফিসারই নিশ্চিত করতে পারেন।’
রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল ঘুরেও দেখা যায় একই দৃশ্য। ঈদের ছুটিতে জরুরি বিভাগে ডাক্তারদের তোড়জোড় থাকলেও ভর্তি থাকা রোগীদের ওয়ার্ডে সিনিয়র ডাক্তারদের আনাগোনা অনেকটাই কম।
হাসপাতালে ভর্তি এক রোগীর স্ত্রী শিল্পী খাতুন (৪৫) বলেন, ‘ডাক্তারদের সেবায় কোনো গাফলতি নেই। কিন্তু শুনছি ঈদে বড় ডাক্তাররা আসবেন না। তাদের দেখলে মনে জোর পাই। তারা না আসলে একটু ভয় ভয় লাগে।’
গোপালগঞ্জ থেকে আসা আরেক রোগীর আত্মীয় মিশকাত (২৮) বলেন, ‘ছুটির মধ্যে সেবা পাচ্ছি, কিন্তু যা পাচ্ছি সেটি আসলে আশানূরূপ নয়। তবে শুনেছি যেকোনো প্রাইভেট হাসপাতালের চেয়ে ঈদের ছুটিতে সরকারি হাসপাতালে সেবা ভালো হয়।’
জরুরি বিভাগে প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসকের উপস্থিতি নিশ্চিত করাসহ জরুরি বিভাগ ও লেবার রুম, ইমার্জেন্সি ওটি (জরুরি অস্ত্রোপচারকক্ষ) ও ল্যাব সার্বক্ষণিক চালু রাখতে দেশের হাসপাতালগুলোকে ১৬ দফা নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হাসপাতালে পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করতে ঈদের আগে ও পরে সমন্বয় করে ছুটি নির্ধারণ করা হবে।
ঈদের তিন দিন বন্ধ সরকারি হাসপাতালের আউটডোর সেবা। এ ব্যাপারে ছুটি শুরুর আগে কথা হয় বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. মাহবুবুল হকের সঙ্গে।
তিনি বলেন, ‘ঈদের আগের দিন, ঈদের দিন ও পরদিন আউটডোর সেবা বন্ধ থাকবে। তবে এর মানেই এই না রোগী আসলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আউটডোরে রোগী আসলে তাদের জরুরি বিভাগের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা হয়। রোস্টার অনুযায়ী জরুরি বিভাগ চলে।’
‘চেষ্টা থাকে ঈদের দিনটা অন্য ধর্মাবলম্বী ডাক্তারদের দিয়ে জরুরি বিভাগ চালানোর। তবে ঈদের ছুটি হোক বা অন্যকিছু, রোগীদের সেবার ক্ষেত্রে মিস ম্যানেজমেন্ট (অব্যবস্থাপনা) এড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে কর্তৃপক্ষের।’
তবে সরকারি হাসপাতালের চেয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে সেবার মান ভালো দাবি করা হলেও ঈদের দিন প্রাইভেট হাসপাতালে ল্যাব কার্যক্রম প্রায়ই বন্ধ পাওয়া যায়—এমন অভিযোগ এসেছে রোগীদের কাছ থেকে।
ভুক্তভোগী এমন একজন রোগী সাব্বির হোসেন (৩৭) বলেন, ‘এক বছর আগে ঈদের দিন অসুস্থ হয়ে পড়ি। সকালে ডাক্তারের পরমার্শ অনুযায়ী ইমার্জেন্সি টেস্টের জন্য কম করে হলেও পাঁচ-ছয়টা হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে হয়েছে। পরে আরেক ডাক্তার আত্মীয়ের মাধ্যমে তদবির করে টেস্ট করানো গেছে।’
প্রাইভেট হাসপাতালে ঈদের আগে রোগীদের একরকম জোরপূর্বক রিলিজ দিয়ে দেওয়া হয়, সিনিয়র ডাক্তাররা আসেন না, নার্সদের সেবা পাওয়া যায় না—এমন সব অভিযোগের ব্যাপারে রাজধানীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডা. খান রাওয়াত বলেন, ‘ঈদের আগে রোগীরা নিজেরাই বাসায় ফেরার জন্য উতলা হয়ে ওঠেন। অনেক সময় ডাক্তারের সাজেশন না মেনেই তারা বাসায় ফিরতে চান। তাদের মনের অবস্থাটাও আমরা বুঝি। কে না চায় নিজ পরিবারের সঙ্গে শান্তিমতো ঈদ করতে! তাই আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে ঈদের আগে খুব সিরিয়াস কিছু না হলে যেসব রোগী রিলিজ চাইছেন, তাদের বাড়ি যেতে দেওয়া।’
তিনি বলেন, ‘অনেকেই মনে করেন, ঈদের দিনে ডাক্তার-নার্স ছাড়া হাসপাতালগুলো বিরানভূমিতে পরিণত হয়। আসলে মোটেও এমন কিছু নয়। নামাজের পর, আবার দুপুরের পর সিনিয়র ডাক্তারা হাসপাতালে এসে ঘুরে যান; রোগীদের খোঁজখবর নেন। সিরিয়াস কিছু হলে মেডিকেল অফিসাররা যখন তখন তাদের (সিনিয়র ডাক্তার) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তাই এটা ভাবার কারণ নেই যে, ঈদ বা ছুটি বলে রোগীদের চিকিৎসাসেবার বিন্দুমাত্র গাফলতি হয়।’
এদিকে, ঈদের দিন হাসপাতালগুলোতে রোগীদের জন্য বিশেষ অ্যাপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।
রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকালে রোগীদের সেমাই খাওয়ানো হয়েছে; সঙ্গে ছিল পাউরুটি, কলা, দুধ, ডিম ও বিস্কুট। দুপুরে পোলাওয়ের সঙ্গে মুরগির রোস্ট, রেজালা, ডিম কোরমা ও কোক দেওয়া হয়। অনেক হাসপাতালে রোগীদের খাওয়া শেষে আপেল কিংবা কমলাও দেওয়া হয়। আর রাতে নিয়মানুযায়ী থাকে ভাত, ডাল ও সবজি।
তবে আপ্যায়ন যেমনই হোক, হাসপাতালে ঈদ কাটানো একেবারেই কাম্য নয় রোগীদের। আর বাধ্য হয়ে যদি হাসপাতালে থাকতেই হয়, তাহলে পূর্ণাঙ্গ সেবার প্রত্যাশা রোগী ও তাদের আত্মীয়দের।